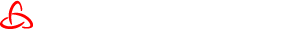শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় শেষ বিদায় জানানো হলো ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিককে

ছবি: প্রতিনিধি, বিডি২৪লাইভ
শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় প্রয়াত ভাষাসংগ্রামী, লেখক ও গবেষক আহমদ রফিককে শেষ বিদায় জানিয়েছেন সর্বস্তরের মানুষ। শনিবার দুপুরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের পর শোকমিছিলসহ মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় রাজধানীর ইব্রাহিম কার্ডিয়াক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও গবেষণার কাজে তাঁর মরদেহ হস্তান্তর করা হয়, যা ছিল তাঁর জীবনের শেষ ইচ্ছা।
ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক ফাউন্ডেশনের আয়োজনে সকাল থেকেই শহীদ মিনারে ভিড় করেন নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ। প্রায় দুই ঘণ্টা সেখানে রাখা হয় তাঁর মরদেহ। ফুলেল শ্রদ্ধা আর অশ্রুসিক্ত চোখে তাঁকে বিদায় জানান শুভানুধ্যায়ীরা।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, "মেডিকেল থেকে পাস করলেও ভাষা আন্দোলনে যুক্ত থাকার কারণে তাঁকে ইন্টার্নি করতে দেওয়া হয়নি। এতে বোঝা যায় তিনি আন্দোলনের সঙ্গে কতটা নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। আহমদ রফিক শুধু ভাষাসংগ্রামী নন, তিনি গবেষক ও লেখকও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তাঁর অসামান্য গবেষণার জন্য কলকাতার রবীন্দ্র গবেষণা কেন্দ্র তাঁকে 'রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য' উপাধি দেয়।"
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহ উদ্দিন আহমদ বলেন, "জাতি এক সূর্যসন্তানকে হারাল। তাঁর জীবন ও কর্ম আমাদের জন্য অনন্ত প্রেরণা হয়ে থাকবে।"
শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি রেজাউদ্দিন স্টালিন বলেন, "আহমদ রফিকের মতো মানুষের মৃত্যুতে জাতি গভীর শোকাহত। তাঁকে মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা উচিত।"
বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম বলেন, "তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আদর্শে অবিচল ছিলেন। মরণোত্তর দেহদান তাঁর মানবিক আদর্শেরই প্রকাশ।"
বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেন, "তিনি ছিলেন এক প্রচারবিমুখ, নির্লোভ ও মানবিক মানুষ। পুরস্কার বা স্বীকৃতির মোহ তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি, এই কারণেই তিনি আজীবন নিজের কমিটমেন্টে অটল থেকেছেন।"
গত বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর একটি হাসপাতালে ৯৬ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আহমদ রফিক। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনি জটিলতা, আলঝেইমার্স ও পারকিনসন্সসহ নানা রোগে ভুগছিলেন।
১৯২৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শাহবাজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। মুন্সিগঞ্জের হরগঙ্গা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাসের পর ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।
আন্দোলনের সময় তাঁকে একমাত্র ছাত্র হিসেবে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার মুখে পড়তে হয়। পরবর্তীতে চিকিৎসা পেশায় না গিয়ে নিজেকে নিবেদিত করেন লেখালেখি ও গবেষণায়। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গ্রন্থ, 'শিল্প সংস্কৃতি জীবন'। তিনি একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ বহু সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।
ভাষা আন্দোলনের এই অকুতোভয় সৈনিকের জীবন ও আদর্শ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।
বিডি২৪লাইভ ডট কম’র প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
পাঠকের মন্তব্য:
সর্বশেষ খবর
জেলার খবর এর সর্বশেষ খবর
- পাস ছাড়াই টিকিট বিক্রি; সেন্ট মার্টিনগামী সিন্দাবাদকে জরিমানা
- মানিকগঞ্জে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে দূর্বৃত্তের আগুন
- কালীগঞ্জে ন্যাশনাল জুট মিল গণহত্যা দিবস: শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের খসড়া দ্রুত অনুমোদনের দাবি
- সৌদিতে বাংলাদেশী কর্মীদের দ্বারা অপকর্ম রুখতে প্রবাসীদের ৭ দফা দাবি