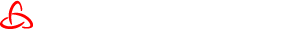প্রচ্ছদ / ধর্ম ও জীবন / বিস্তারিত
ইসলামের দৃষ্টিতে ভোট দেয়া বৈধ নাকি অবৈধ?
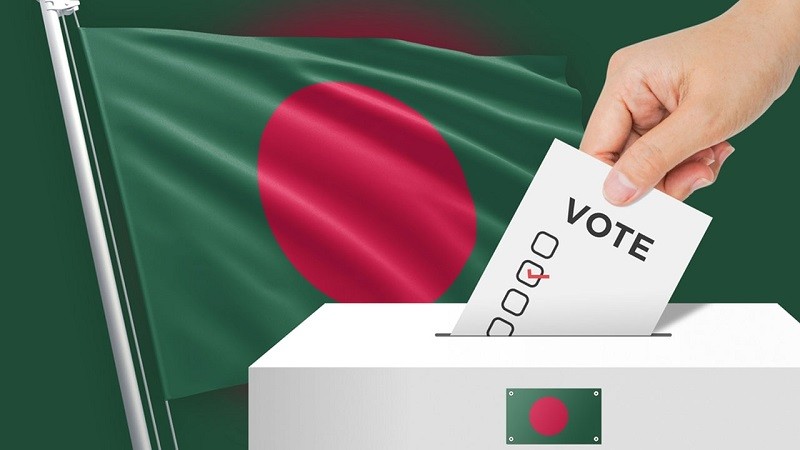
ছবি: সংগৃহীত
ইসলামে শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, আধুনিক গণতন্ত্রের পূর্ণ কাঠামো ইসলামের আদর্শের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
গণতন্ত্রে মূলত সংখ্যার ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা মানুষের হাতে থাকে। ইসলামী দার্শনিকরা মনে করেন, এটি আল্লাহর সার্বভৌম শাসনাধিকারের সঙ্গে সংঘর্ষ সৃষ্টি করতে পারে।
ইসলামিক আইনবিজ্ঞান (শরিয়াহ) বলছে, মানবসৃষ্ট আইন কখনো আল্লাহর বিধানকে সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপন করতে পারে না। তবুও ইসলামে নেতৃত্ব নির্বাচন এবং সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি সুপ্রাচীন ধারণা বিদ্যমান।
কুরআনে উল্লেখ আছে, “তোমরা তাদের মধ্যে যেসব বিষয়ে বিতর্কে পড়বে, তাদের মধ্যে পরামর্শ করো” (সূরা আল‑শূরা, ৪২:৩৮)।
শূরা বা পরামর্শভিত্তিক এই নীতি ইসলামী রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ভিত্তি স্থাপন করেছে। এখানে প্রধান বিষয় হলো, সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতা নয়, প্রার্থীর যোগ্যতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং মুসলিম সমাজের কল্যাণকে প্রধান্য দেওয়া।
প্রখ্যাত ইসলামি স্কলার ড. ইউসুফ আল‑কারদাবি উল্লেখ করেছেন, গণতন্ত্র পূর্ণরূপে ইসলামের শাসনব্যবস্থার সমতুল্য নয়। তবে শূরার নীতির সঙ্গে কিছু দিককে সমন্বয় করা সম্ভব।
তার মতে, সৎ ও দায়িত্বশীল নির্বাচনী প্রক্রিয়া সমাজে ন্যায়, হিসাবদায়িত্ব এবং জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে। এই অংশগ্রহণ যদি আল্লাহর বিধান, ন্যায় ও শারিয়াহ অনুযায়ী সীমাবদ্ধ থাকে, তবে এটি ইসলামী নৈতিকতা অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য।
অন্যদিকে, শায়খ আশরাফ আলি থানভী এবং অন্যান্য ঐতিহ্যগত স্কলার গণতন্ত্রকে সরাসরি সমর্থন করেননি। তাদের যুক্তি হলো, সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত সবসময় ন্যায়সংগত হয় না এবং কখনও কখনও তা ইসলামী নীতির বিরুদ্ধে যায়। তবে তারা স্বীকার করেন যে ভোট প্রদানের মাধ্যমে অংশগ্রহণ একটি ন্যায্য মাধ্যম হতে পারে, বিশেষ করে যদি উদ্দেশ্য থাকে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচন করা।
ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে হানাফি, মালিকি, শাফি ও হাম্বলি চারটি মাযহাবেও দেখা যায়, শাসক নির্বাচনের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও ন্যায়কে প্রধান্য দেওয়া হয়েছে।
হানাফি মাজহাব শূরা ও পরামর্শভিত্তিক নির্বাচনের দিকে গুরুত্ব দিয়েছে। মালিকি ও শাফি ইমামরা বলেছেন, সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করতে সৎ ও যোগ্য নেতা নির্বাচিত হওয়া আবশ্যক।
হাম্বলি ইমামও নির্দেশ দিয়েছেন, শাসককে অবশ্যই ন্যায়ের পথে পরিচালিত হতে হবে। এই শিক্ষাগুলো প্রমাণ করে যে ভোটদান একটি মাধ্যম হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে যদি তা ন্যায় ও ইসলামী মূল্যবোধকে অক্ষুণ্ণ রাখে।
মুফতি মুহাম্মাদ শফী (রহ.) এ সংক্রান্ত একটি পুস্তিকায় লিখেছেন যে, ইসলামের দৃষ্টিতে ভোট হচ্ছে তিনটি বিষয়ের সমষ্টি। ১. সাক্ষ্য প্রদান ২. সুপারিশ ও ৩. প্রতিনিধিত্বের অথরিটি প্রদান।
কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল সবারই জানা রয়েছে যে, শরীয়তে উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, কোনো ব্যক্তিকে রাষ্ট্রীয় নীতিমালা তৈরির এবং রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য প্রতিনিধিত্বের সনদ দেওয়ার মানে হচ্ছে প্রতিনিধিত্ব দানকারী (ভোটার) তার ভবিষ্যত সকল কার্যকলাপের দায়িত্ব নিজ কাঁধে নিচ্ছে।
এমনিভাবে সুপারিশের বিষয়টিও প্রনিধানযোগ্য। কুরআনুল কারিমের ভাষায় ‘যে ভালো সুপারিশ করবে সে তার নেকীর ভাগী হবে। আর যে মন্দ সুপারিশ করবে সেও মন্দের হিস্যা পাবে।’ সুরা নিসা, আয়াত ৮৫
সুতরাং, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ভোট প্রদান একটি সূক্ষ্ম ও দায়িত্বপূর্ণ বিষয়। যদিও গণতন্ত্রের পুরো কাঠামো ইসলামের আদর্শের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল রাখে না, তবুও ভোট প্রদানের প্রক্রিয়া যদি শূরা, ন্যায় এবং শারিয়াহের মূল্যবোধকে সম্মান করে, তবে এটি মুসলিমদের নৈতিক দায়িত্ব এবং সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।
এটি একটি মধ্যম পথ, যেখানে ইসলামী নীতি এবং অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া একে অপরকে পরিপূরক করে।
কুশল/সাএ
বিডি২৪লাইভ ডট কম’র প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
পাঠকের মন্তব্য:
সর্বশেষ খবর