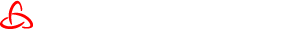আপনাকে আমরা কেন ভোট দিব?

ছবি: গ্রাফিক্স আর্ট
বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে 'আপনাকে আমরা কেন ভোট দিব?'—এই প্রশ্নটি এখন আর কেবল একজন ভোটারের কৌতূহল নয়, এটি আমাদের সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি কোটি নাগরিকের হতাশা ও আস্থার সংকটের প্রতিচ্ছবি।
বিশেষত যখন নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি আর তার বাস্তবায়নের মধ্যে বিস্তর ফারাক তৈরি হয়, তখন এই প্রশ্নটি একটি অনিবার্য দাবিতে পরিণত হয়।
গত বছরের ৫ই আগস্টের ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান প্রমাণ করেছে, জনগণ যখন মৌলিক আস্থাহীনতায় ভোগে, তখন তারা নিজেই পরিবর্তনের চালক হয়ে ওঠে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ ছিল দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও জবাবদিহিতাহীনতার বিরুদ্ধে একটি রায়। প্রশ্ন হলো, সেই বিপুল পরিবর্তনের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো কি জনগণের এই জিজ্ঞাসা মেটাতে প্রস্তুত?
প্রতিশ্রুতি বনাম প্রতারণার ফাঁক
আমাদের রাজনীতিতে একটি চিত্র বারংবার ফিরে আসে: ভোটের আগে আকাশচুম্বী প্রতিশ্রুতি। প্রার্থীরা নিজেকে জনগণের সেবক হিসেবে উপস্থাপন করেন, তুলে ধরেন উন্নয়ন, সুশাসন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের অঙ্গীকার। কিন্তু ম্যান্ডেট পাওয়ার পর বহু নেতাই জনসেবার পরিবর্তে ক্ষমতাকে ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং দলীয় স্বার্থ রক্ষায় নিবদ্ধ করেন।
জনগণের সঙ্গে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। নির্বাচনী ইশতেহার তখন শুধুই 'ভুলে যাওয়া নথি'তে পরিণত হয়। এই 'প্রতিশ্রুতি ও প্রতারণার ফাঁক'-ই সাধারণ ভোটারদের মনে সবচেয়ে বড় আস্থাহীনতা তৈরি করেছে। জনগণ তখন নিজেকে কেবল 'ভোট দেওয়ার যন্ত্র' হিসেবেই আবিষ্কার করে।
অর্থের বিনিয়োগ এবং ক্ষমতার পুনরাবৃত্তি
বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে অর্থের প্রভাব একটি ওপেন সিক্রেট। আপনার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী: রাজনৈতিক ব্যক্তিরা ভোটের মাঠে প্রচুর টাকা খরচ করেন, যার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে পরবর্তীতে এই টাকার কয়েকগুণ থেকে কয়েকশো গুণ পর্যন্ত অর্জন করা। এই বিপুল ব্যয়কে তারা 'বিনিয়োগ' হিসেবে গণ্য করেন। আর এই বিনিয়োগের মুনাফা তোলা হয় ক্ষমতা ব্যবহার করে—টেন্ডার, নিয়োগ, প্রভাব বিস্তার এবং দুর্নীতির মাধ্যমে।
এই প্রবণতা সৎ ও যোগ্য প্রার্থীদের কোণঠাসা করে দেয় এবং রাজনীতিকে বিত্তশালী ও সুবিধাভোগী শ্রেণির হাতে তুলে দেয়। ৫ই আগস্টের পর যখন ক্ষমতা থেকে যাওয়া দলের আর্থিক অনিয়ম নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, তখন নতুন রাজনৈতিক শক্তিগুলোর প্রতি জনগণের প্রত্যাশা ছিল, তারা এই ধারা থেকে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বিভিন্ন দলের সাংগঠনিক কাঠামো ও ভবিষ্যৎ নির্বাচনী পরিকল্পনায় সেই পুরাতন 'অর্থের খেলা'র ইঙ্গিতই মিলছে। এটিই এখন জনগণের মনে বড় জিজ্ঞাসা—নতুন নেতারা কি কেবল পুরাতন পথে হাঁটতে এসেছেন?
৫ই আগস্টের পর কেন এই প্রশ্ন?
৫ই আগস্টের অভ্যুত্থান ছিল কেবল একটি দলের বিরুদ্ধে নয়, বরং ছিল দুর্নীতি, অগণতান্ত্রিকতা ও জবাবদিহিতাহীনতার বিরুদ্ধে। কিন্তু যদি দেখা যায়, আওয়ামী লীগের মতো আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দল একই পথে হাঁটছে—যদি ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা ব্যক্তিরা সংস্কারের চেয়ে ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করতে ব্যস্ত থাকেন, যদি তারা এখনো অর্থ ও পেশিশক্তির ওপর নির্ভর করেন, তবে জনগণ প্রশ্ন করতে বাধ্য:
"আপনাকে কেন ভোট দেব? আপনারা যদি পুরাতন মানসিকতা ও পুরাতন পথে হাঁটতেই আসেন, তবে পরিবর্তনের অর্থ কী?"
জবাবদিহিতার অঙ্গীকারই হোক উত্তর
জনগণের এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর রাজনীতিবিদদেরই দিতে হবে। সেই উত্তর কেবল কথার ফুলঝুরিতে নয়, বরং কার্যক্রমে প্রতিফলিত হতে হবে।
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা: ক্ষমতাকে ব্যবহার করে ব্যক্তিগত মুনাফার পথ বন্ধ করতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা: নির্বাচন কমিশন, বিচার বিভাগ ও প্রশাসনকে দলীয় প্রভাবমুক্ত রেখে শক্তিশালী করতে হবে।
সৎ নেতৃত্ব: অর্থের দাপট নয়, আদর্শ ও জনসেবাকেই রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি করতে হবে।
যে রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তি ৫ই আগস্টের চেতনা ধারণ করে, পুরাতন মডেলের রাজনীতি বর্জন করে, এবং জনগণের প্রতি সত্যিকার অর্থে দায়বদ্ধ থাকার অঙ্গীকার করে, কেবলমাত্র তাকেই জনগণ ভোট দিতে প্রস্তুত। যতদিন না এই মৌলিক পরিবর্তন আসে, ততদিন "আপনাকে আমরা কেন ভোট দিব?"—এই প্রশ্নটি বাংলাদেশের রাজনীতির ব্যর্থতার প্রতীক হিসেবেই আমাদের সামনে জ্বলন্ত থাকবে।
লেখক: আমিরুল ইসলাম আসাদ
এডিটর-ইন-চিফ
বিডি২৪লাইভ ডট কম।
(খোলা কলাম বিভাগে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব। বিডি২৪লাইভ ডট কম-এর সম্পাদকীয় নীতির সঙ্গে প্রকাশিত মতামত সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে।)
সালাউদ্দিন/সাএ
বিডি২৪লাইভ ডট কম’র প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
পাঠকের মন্তব্য:
সর্বশেষ খবর
খোলা কলাম এর সর্বশেষ খবর